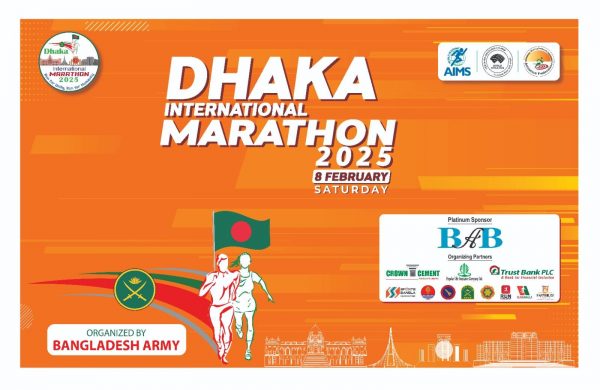ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান
- আপডেট টাইম : মঙ্গলবার, ৩ আগস্ট, ২০২১, ১২.১৩ এএম


বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুফি-সাধক, সমাজ-সংস্কারক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি শিক্ষাদান ও শিক্ষা-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে বাংলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।
এক সমীক্ষায় দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ববাংলার শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিতের হার ৬ থেকে ৭ শতাংশের বেশি ছিল না। এই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যে মুসলিম ছাত্রের শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ১৪.৪ শতাংশ, যা তৎকালীন মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে ৪ থেকে ৫ শতাংশের মতো। ১৯০৬-০৭ সালে সারা পূর্ববঙ্গ ও আসামে এফএ পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের মধ্যে ১২ জন (৪.৩ শতাংশ) এবং স্নাতকদের মধ্যে মাত্র একজন (২.৪ শতাংশ) ছিল মুসলমান। ১৯১১-১২ সালে মুসলমান স্নাতকদের হার ছিল ১১.৩ শতাংশ (কলা) ও ৯.৬ শতাংশ (বিজ্ঞান)।
শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র কর্মকর্তা থাকা অবস্থায়ই ১৯১১ সালে তিনি শিক্ষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খানবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং একই বছর মেম্বর অব দ্য রয়্যাল এডুকেশন সোসাইটির পদ লাভ করেন। ১৯১৭-১৮ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন ফর মোহামেডান পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমির ফেলো পদ লাভ করেন।
১৯১২ সালের পর থেকে সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত যত কমিটি, কমিশন, টেকনিক্যাল সম্মেলন হতো সেগুলোয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতেন।
১৯১৪ সালের পর থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম প্রণয়নের জন্য গঠিত নাথান কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মতে, শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে, যাতে মানুষের সৃজনশীলতা বিকশিত হয়, মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট হয়, যাতে জ্ঞানের অন্বেষণ ও সুপ্তশক্তি বিকাশের ধারা সূচিত হয়, জ্ঞানলিপ্সাকে বর্ধিত করে।
মুসলমান সমাজের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে ১৮৩৪ সালে ফারসি ভাষার পরিবর্তে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনকে দায়ী করা হয়। এতে করে মুসলমান সমাজ ইংরেজি বিজাতীয় ভাষা হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের বিরত রাখে। ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার কারণে মুসলমান জনগোষ্ঠীর আর্থিক অসচ্ছলতা, চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সামাজিকভাবে অবহেলার শিকার হতে হয়।
এই প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন, ‘অতীতে আমরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি, পুনরায় সেরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। হিন্দু ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে হইলে মোছলমান ছাত্রের জন্য যথোপযুক্ত উদার শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই শিক্ষার প্রতি যাহাতে মোছলেম অভিভাবকমণ্ডলীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও অতীব প্রয়োজন।’ এই সময়ে মুসলমান সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতীফ, নওয়াব ফয়জুননেসা চৌধুরাণী, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। স্যার সৈয়দ আহমদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরেরও চেষ্টা করেন।
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। ১৯১৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নোবেল, কালজয়ী উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের অমর কথাসাহিত্যিকের স্বীকৃতি লাভ, গ্রামণ্ডবাংলার মাটি ও মানুষের সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম বর্ণনার কাব্যময় পরিবেশনে পল্লীকবি জসিমউদ্দীন, বিদ্রোহের বীণা হাতে কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), কালজয়ী সাহিত্য রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলী এবং নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত যখন বাংলার সাহিত্য আকাশে জ্বলজ্বল করছে, তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এক ভিন্নধর্মী সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে নীরবে-নিভৃতে সমাজের সেবা করে গেছেন।
তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মতান্তরে ৭৯টি। ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মতে, বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাস, ধর্মব্যাখ্যাতা, সমাজতান্ত্রিক ভাবুক ও সামাজিক, অগ্রগতির এক বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক হিসেবে আহ্ছানউল্লার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ড. মুস্তফা নূরউল ইসলামের মতো আহ্ছানউল্লা আর এক বিদ্যাসাগর। আহ্ছানউল্লার সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনি প্রেমের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেণির মানুষকে দেখেছিলেন। লেখক হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যদিও একটু আড়ালে পড়ে থাকেন, তার কারণ নির্জন সাধনাকেই তিনি নিজের পথ বলে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার তর্ক-সমাচ্ছন্ন কোলাহল থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিমুক্ত।
মানবতাবাদ ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন, ‘আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না। শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় প্রভেদ দেখি না, ছোট-বড় বুঝি না, সবাই শক্তিমান দয়াময় স্রষ্টার সৃষ্টি। আমি কাহাকে ক্ষুদ্র বলিবো, কাহাকে কাফের ডাকিবো, কাহাকে ঘৃণা করিবো।’
আন্তঃধর্ম সম্প্রীতির উপায় ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ‘জগতের বিভিন্ন ধর্ম, প্রত্যেক ধর্মেরই মূলনীতি এক। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করেছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। বৈষ্ণব ধর্ম বলে, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। ইসলাম বলে, সৃষ্টের সেবায়ই স্রষ্টার রূহ বিদ্যমান। পার্সিক ধর্ম বলে, যারা সবার শান্তি কামনা করে, তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান। প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই উপাসনার নির্দেশ আছে। কেহ সাকার উপাসনা করে, কেহ নিরাকার উপাসনা করে।’
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনায় ব্রত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর রচিত ৭৯টি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র দুটি বই ইংরেজিতে রচনা করেন। অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ। তাই ১৯১৮ সালে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, মাতৃভাষা এবং স্বদেশভূমি বিষয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, ‘ভাই সকল, হিন্দু-মুসলমানি দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভুলিয়া যাও।’
বঙ্গভঙ্গের পর তাঁর উচ্চারণ, ‘বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক। ভাষার যতই ভেদ হইবে, শ্রেণিগত পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় জীবনের ততই লোপ পাইবে। সাহিত্যের ততই অবনতি ঘটিবে।’
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে কোলকাতা কেন্দ্রিকতার স্বার্থমূলে আঘাত আসে, ভিত কেঁপে ওঠে সামন্তবাদী মনোভাবের, এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সূচিত হয়। বিভক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং তা সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়, সেটাই মুসলিম জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ঘটাতে এবং তাদের স্বতন্ত্রবাদী রাজনীতিতে যোগদানে অনুপ্রাণিত করে এবং ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্মলাভ হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত সরকার দরবার দিবসে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। একই সালে কোলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।
বঙ্গভঙ্গরোধকে পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজের স্বপ্নভঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করেন একে ফজলুল হক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের এক অধিবেশনে ফজলুল হক যে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বীজ সেখানেই উপ্ত হয়।
১৯১২ সালের ২৭ মে তারিখে সরকার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে রেজুলিউশন জারি করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলমান সুধী ও সুশীল সমাজের যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে নবাব সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হুদা, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মৌলবী আবদুল করিম, নবাব সলিমুল্লাহ, একে ফজলুল হক, শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতারা ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তার কাছে বিভিন্ন দাবি পেশ করেন। সেদিনই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের জন্য একজন শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। লর্ড কার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন একে ফজলুল হক। ১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন।
নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৪ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সি মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বিলম্বের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলে বাংলার ডিপিআইডব্লিউডব্লিউ হর্নেলের নেতৃত্বে বাংলা সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধানে যে কমিটি গঠন করে, তাতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অন্যতম সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘এক বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া উক্ত কমিটি ১৯৭টি রেজুলিউশনসহ এক কার্য্যবিবরণী পেশ করেন। …. ঐ সময়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ফলাফল আশাপ্রদ হয় নাই। কমিটির সর্বোপেক্ষা প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত হয় নাই।’
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত সংগ্রহ কমিটির কাছে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যে কয়টি বিষয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করেন, তার মধ্যে তিনি প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির এখতিয়ার এবং কীভাবে অর্পিত দায়িত্ব স্থানান্তর বা সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসিত হতে পারে, তার রূপরেখা স্পষ্ট করেন।
ওই কমিশনের ১০ নম্বর জিজ্ঞাসা ছিল- তাঁর শিক্ষা পরীক্ষা-সংক্রান্ত আর কোনো মতামত আছে কি না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর অভিমতে বলেন, ‘বিদ্যমান ব্যবস্থা ভালো, তবে পরীক্ষকের খাতা দেখার ব্যাপারে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হবার অবকাশ আছে।’ উল্লেখ্য, তাঁরই প্রচেষ্টায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় খাতার প্রথমবারের মতো নামের পরিবর্তে রোল নম্বর প্রথা প্রচলিত হয়। ১১ নম্বর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি ইংরেজি ভাষা চর্চার অনিবার্যতাকে তুলে ধরেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল ১৯১৯ বিবেচনার জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একমাত্র বাঙালি মুসলমান সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হইলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয়, পরে উহা বিবেচনার জন্য একটা স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। উহার মধ্যে আমি একজন মেম্বর ছিলাম এবং যতদূর সাধ্য উহার আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছিলাম।’
উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে অর্থাৎ ১৯২১ সালে বাংলায় আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর বিশ্বভারতী (১৯২১) এবং একই সালে কোলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
ড. মো. আবদুল মজিদ তাঁর ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপর্বে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা’ শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে বলেন, ‘বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃজিতে সমস্যা, বাধাদানে গৃহীত ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে পূর্ববঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণবহ না হতে পারে, সে ব্যাপারে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মুখে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী পর্ষদসমূহের একমাত্র পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সদস্য হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অবিসংবাদিত ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাবীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই পূর্ববঙ্গের জনগণ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হয়, মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ এবং স্বাধিকার থেকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফল হয়।’
সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ‘স্রষ্টার এবাদত-সৃষ্টের সেবা’- এই মর্মবাণীকে হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৯৩৫ সালে নলতা আহ্ছানিয়া মিশন এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো আজ মানবসেবায় দেশের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থনা, প্রতিষ্ঠানটি যেন হাজার বছর ধরে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী থেকে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস অব্যাহত রাখে।
লেখক : কাজী রফিকুল আলম,
সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন