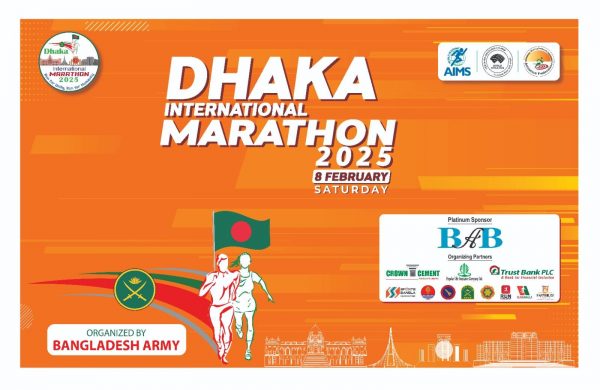বুক না ছুঁয়ে রোগ চেনার কথা..
- আপডেট টাইম : বৃহস্পতিবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২২, ৮.৪৪ এএম
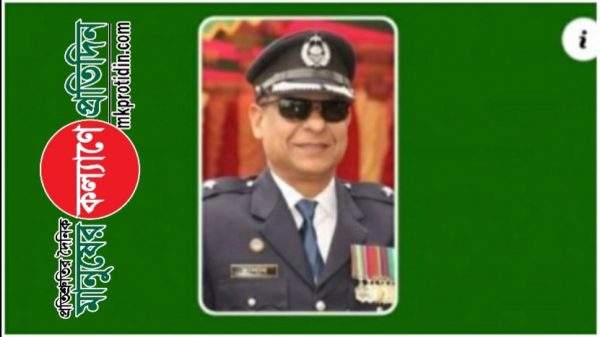
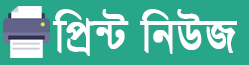
ডাক্তার চেনার সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত উপায় হচ্ছে গলায় ঝোলানো স্টেথোস্কোপ। হার্ট সাউন্ড ব্রেথ সাউন্ড শোনার পাশাপাশি আজ তা চিকিসৎকের অঘোষিত আইডিও বটে…
দু’শতাব্দি আগের কথা, তখনকার দিনে রোগীর হৃদস্পন্দন, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে রোগীর বুকে পাঁজরে কিংবা পিঠে কান লাগাতে হতো। দেহের অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনার এই পদ্ধতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Immediate Auscultation বলে।
১৮১৬ সালের কথা, প্যারিসের ন্যাকার হাসপাতালের চীফ ফিজিশিয়ান ডাঃ রেনে লেনেক (René-Théophile-Hyacinthe Laennec) এর কাছে হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে এলেন এক ডাবল এক্স এল তরুণী, হার্টের সমস্যা তাই বুকের ভেতরের শব্দ না শুনে তো রোগ আঁচ করা যায় না। এমনিতেই স্থুল, তার উপর পরনে মোটা বসন! তা না খুলে কি করে রোগিনীর বুকে কান পাতবেন তা ভেবেই অকৃতদার ডাক্তার বাবু তো লজ্জায় লাল…!
ভাবতে লাগলেন লেনেক বাবু, হঠাৎ মনে পড়লো কিছুদিন আগে স্কুলের কিছু বাচ্চাকে কাঠের চোঙ নিয়ে খেলতে দেখেছিলেন। তাদের একজন ফাঁপা কাঠের এক প্রান্তে ঘসা দিয়ে শব্দ তৈরী করছিল আর আরেক পাশে কান পেতে অন্যরা সে শব্দ শুনে মজা করছিলো। ভেবে দেখলেন, ফাঁপা চোঙ শব্দকে এ্যামপ্লিফাই করছে। কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ প্রবাহিত হলে তা বহুগুণে বেড়ে যায়। বুদ্ধি খেলে গেলো, বিষয়টা রোগী পরীক্ষার কাজে লাগানো যায় কিনা…
ব্যাস, হাতের কাছে থাকা কাগজের নোটবুক পেঁচিয়ে বানিয়ে ফেললেন চোঙা, তার এক পাশ রোগিণীর বুকে আর অন্য পাশ নিজের কানে লাগিয়ে টের পেলেন শব্দগুলো আগের চেয়েও ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে। সোজা ছুটলেন ওয়ার্ডে, একে একে সব রোগীকে সেই চোঙা দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হাজার খানেক রোগী পরীক্ষা করে কয়েক বছরের মধ্যে রোগভেদে শব্দগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগও করে ফেললেন, সাথে প্রত্যেকটা শব্দের প্রকৃতি আলাদাভাবে বর্ণনা করলেন। আজ যা (Rhonchi, Crepitance, Rales, Egophony, etc) বলে পরিচিত, এগুলোর অধিকাংশই লেনেকের ব্যাখ্যা করা। তিনিই Immediate Auscultation এর পরিবর্তে Mediate Auscultation বিষয়টা সবার নজরে আনেন।
কাজের সুবিধার্থে সবসময় ব্যবহারের জন্য তিনি ২৫ সে মি লম্বা আর ২.৫ সে মি প্রস্থ বিশিষ্ট একটি কাঠের ফাঁপা নল বানিয়ে নেন। দুটি গ্রীক শব্দ ,“Stethos”যার অর্থ বুক আর “Skopos” মানে অনুসন্ধান করা, জুড়ে দিয়ে নাম রাখলেন স্টেথোস্কোপ (Stethoscope)। ১৮৪০ সালে Golding Bird এতে ফ্লেক্সিবল টিউব ব্যবহার করেন, তবে তা এক কানেই ব্যবহার করা হতো। এরপর ১৮৫১ সালে আইরিশ চিকিৎসক Arthur Leared দুই কানে ব্যবহার্য মডেল আবিষ্কার করেন।পরের বছর George Phillip Cammann মডেলটাকে আরেকটু উন্নত করেন যা ১৮৫২ সালে বাজার জাত শুরু হয়, এখন পর্যন্ত সেই মডেলটাই স্ট্যান্ডার্ড মডেল।
এরপর যক্ষা রোগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সে রোগেই আক্রান্ত হন তিনি। তাঁর রোগটি সনাক্ত হয় তাঁরই আবিস্কার করা স্টেথোস্কোপ ব্যবহারে। মৃত্যুর আগে তাঁর সব গবেষণাপত্র, ঘড়ি আংটি আর এই স্টেথোস্কোপ যাকে The greatest legasy of my life আখ্যায়িত করে উইল করে দিয়ে এই নিঃসন্তান।
তবে বুকে কান না ঠেকিয়ে রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি তৎকালিন অনেক চিকিসৎকই, তারা এটিকে হাস্যকর ও নির্ভরযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেন..!!!
লেখকঃ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীর আইন প্রশিক্ষক হাসান হাফিজুর রহমান।